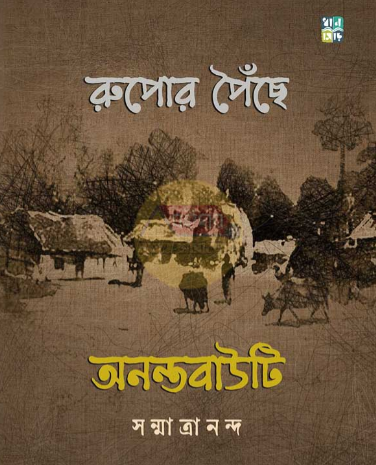সমিধশংকর চক্রবর্তী
আমাদের ধর্ম, আমাদের সভ্যতা যতবার পাপবিদ্ধ হয়েছে, ততবার সেই সকল কলুষ হরণ করে মানবতার ঋতপথ পথিকৃতের মতো যাঁরা আমাদের দেখিয়ে দিলেন, যাঁরা আমাদের স্মরণ করালেন আমাদেরই অন্তরে বিরাজমান দেবত্বের কথা, মানুষকে যাঁরা ‘অমৃতের পুত্র’ বলে স্বীকৃতি দিলেন― আমরা তাঁদের ‘অবতার’ বলে মানি। স্বয়ং ঈশ্বর অবতারের শরীর ধারণ করে মানুষের মাঝে অবতীর্ণ হন, জীবন অতিবাহিত করেন। সেই অবতার জীবনে বাল্যলীলা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।
সম্প্রতি ধানসিড়ি প্রকাশন থেকে প্রকাশিত সন্মাত্রানন্দের ‘রুপোর পৈঁছে অনন্তবাউটি’ গ্রন্থে সংকলিত উপন্যাসদ্বয় তেমনই অবতার জীবনের বাল্যলীলার উপরই আধারিত। ‘রুপোর পৈঁছে’ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের এবং ‘অনন্তবাউটি’ উপন্যাসটি জগজ্জননী শ্রীমা সারদাদেবীর শৈশবের আখ্যানমঞ্জরী। যে জ্যোতির্ময় আলোকবর্তিকা হয়ে অবতার তাঁর মানবশরীর ধারণ করেন, অকাতরে প্রেমডোরে বেঁধে রাখেন আপামর মানুষকে, জীবনীগ্রন্থ সেই আলোকধৌত করুণার কথা বলে। পাপ-তাপ-শোকদগ্ধ যত মানুষ সেই অবতারের সান্নিধ্যে, তাঁর কৃপায় ধন্য হন, জীবনীগ্রন্থ নক্ষত্রের আলোয় সেসব মানুষকে দেখে। কিন্তু এই গ্রন্থ তো জীবনী নয়। নয় বলেই অতীত সময়ের অনুপুঙ্খ পটচিত্র রচনার অনন্ত পরিসর সন্মাত্রানন্দ পেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। সেই সময়কার সমাজ- রাষ্ট্রনীতি- অর্থনীতি- জীবনধারা কোনো কিছুই বাদ যায়নি তাঁর সচেতন দৃষ্টি থেকে।
সন্মাত্রানন্দের লেখায় কালের মিলন ঘটে; অতীত-বর্তমানের মধ্যে সাঁকো তৈরি করেন তিনি। এই উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। গতায়ু যুগকে আমাদের সামনে আনতে সন্মাত্রানন্দ তাই মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন প্রাচীন বাংলার জনপ্রিয় কথক ঠাকুরকে। তাঁর গ্রন্থে বালক শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থাৎ গদাধরের কথা শোনাচ্ছেন চিনুশাঁখারি, বালিকা সারদাদেবী অর্থাৎ সারুর কথা লেখক-কল্পিত চরিত্র জয়গোপাল ঘোষের কথায়। প্রসঙ্গক্রমে উঠে আসছে ধাত্রীমায়ের কথা। এইসব কথক বা ধাত্রী চরিত্রেরা প্রত্যক্ষ করেছেন গদাধর-সারুর অপার্থিব শৈশব, অনুভব করেছেন তাঁদের ঐশী সত্তাকে। কিন্তু যে ভগবৎলীলার জন্য ভাবীকাল অপেক্ষমান, তা যে তাঁদের জীবদ্দশায় দেখা হবে না― এই অতৃপ্তি, এই অপূর্ণতা এ জীবনে অখণ্ডনীয় বুঝে আলোচ্য দুই দেবশিশুর পরমপদে তনু-মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে তাঁরা ধন্য হয়েছিলেন। দৈবীভাবের সাথে মানবভাবের এক অদ্ভুত সমন্বয় উপন্যাসের পাতায় পাতায়। গদাধরকে আমরা কখনো দেখি শৈশব থেকেই ঈশ্বরচিন্তায় ভাবতন্ময় এক বালক, তো কখনো আবার মানিকরাজার আমবাগানে ক্রীড়ারত বালকদলের সে-ই নেতা। অন্যদিকে, যিনি এরপর সৎ-অসৎ নির্বিশেষে আপামরের জন্য পেতে দেবেন জননীর কোল, সেই সারদার মাতৃভাবের প্রকাশ যে শৈশব থেকেই বিদ্যমান ছিল, তার নিদর্শন আটপৌরে জীবনের নানা ঘটনায় সন্মাত্রানন্দ তুলে ধরছেন।
ঔপন্যাসিকের আড়ালে সন্মাত্রানন্দ যেন এক চিত্রকর। অপরূপ বর্ণনায় চিত্রায়িত করেছেন গ্রাম বাংলার নৈসর্গিক শোভা, সহজ সরল মানুষের গ্রাম্য জীবনযাত্রা। এই উপন্যাসে কামারপুকুর-জয়রামবাটি গ্রামের কথা তো স্বাভাবিক ভাবে থাকবেই, কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে সন্মাত্রানন্দ তুলে ধরেছেন পার্শ্ববর্তী আরো সকল গ্রামের কথা দেড়ে, সরাটিমায়াপুর, ভুরসুবো, শিহড় ইত্যাদি। আমাদের মানসভ্রমণে যেমন নিয়ে গেছেন লাহাবাবুদের পান্থশালা, মোড়ল পাড়ার সিংহবাহিনী, যুগীদের শিবমন্দির, আনুড়ের বিশালাক্ষী মন্দির, লক্ষ্মীজলা, ভূতির খাল, বুধুই মোড়লের শ্মশান, তেমনই প্রাচীন গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির অঙ্গ যাত্রার আসর, হাট, রাস-ঝুলন-শিবরাত্রির পরবের সাথে আমাদের পরিচয় করাচ্ছেন। কত পুষ্করিণীর শীতলমায়া জড়ানো সেইসব গ্রাম― হলদেপুকুর, হালদারপুকুর, পুণ্যিপুকুর, বাঁড়ুজ্জেপুকুর, আহেরপুকুর ইত্যাদি। বস্তুত, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার বাল্যকাল কেন্দ্রে থাকলেও সন্মাত্রানন্দের এই উপন্যাসগ্রন্থ আসলে সামান্য চাষাবাদ ও পূজার্চনাকে সম্বল করে কামারপুকুর ও জয়রামবাটির চট্টোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়― এই দুই সাত্ত্বিক পরিবারের অনাড়ম্বর যাপনচিত্র, দুঃখ-সুখের, উত্থান-পতনের নানা অধ্যায়মন্ডিত বিস্তৃত কাহিনী।
সন্মাত্রানন্দের লেখায় যে চেতনা কাজ করে তা হল, একজন মানুষ কালবিচ্ছিন্ন কোনো একক সত্তা নন। তাঁর অতীত যেন তাঁরই মধ্যে প্রবাহিত, আবার তিনিই তাঁর ভাবীকালের জন্ম দেন। গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম প্রসঙ্গে তাই সন্মাত্রানন্দ স্মরণ করছেন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লার পরাজয়, ভারতে বিদেশী বণিকের শাসনের পত্তন, ডাচ ও ফরাসীদের পরাস্ত করে ধীরে ধীরে ব্রিটিশের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদ দখল, রাজস্ব ব্যবস্থার ফলস্বরূপ বাংলায় ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণির অত্যাচারের পটভূমি। যে করাল দুর্ভিক্ষের সাক্ষী হয়েছিল বঙ্গদেশ, সন্মাত্রানন্দের লেখায় উঠে এসেছে তাও। বন্ধ পাঠশালা, বন্ধ মন্দির, বন্ধ হাট-বাজার। শ্মশানে শ্মশানে শুধু শৃগাল-কুকুর-শকুনের উল্লাস। সন্মাত্রানন্দ দেখাচ্ছেন ক্ষুধার জন্য মানুষ যতটা অসহায়, ততটাই বেপরোয়া। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে বাংলার কৃষিতে ভিক্টোরিয়ার রাজস্ব-নীতি যেভাবে প্রভাব ফেলেছিল, তেলেঙ্গানা কমিটির মারফৎ প্রচুর খাদ্যশস্যের রপ্তানি যেভাবে বাংলার জনজীবনে ডেকে এনেছিল খাদ্যের সংকট, মূল্যবৃদ্ধির বোঝা― দুর্ভিক্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে করতে সন্মাত্রানন্দ তুলে ধরছেন সেই সব দলিল। গ্রাম বাংলায় ধর্মঠাকুরের পূজার প্রসঙ্গে উঠে এসেছে পাল-সেন রাজবংশের কথা, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণের ইতিহাস। যে অতীত এই উপন্যাসের বিষয়, তখন বাল্যবিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল। বস্তুত, গদাধর-সারুর বিয়েও তো তাই-ই। তবু এই দেবদম্পতির বিবাহকে কেন্দ্র করে সন্মাত্রানন্দ আলোচনা করছেন বল্লাল সেনের রাজত্বকাল, কুলীনপ্রথা, সতীদাহ রদ, বিদ্যাসাগর কৃত বিধবাবিবাহ আইন পাশ, বহুবিবাহ রদ, নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি সংস্কারসমূহ। ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্রে রেখে সময়ের বিস্তৃত ব্যসার্ধে এভাবে ইতিহাসের চরাচর জরিপ আসলে ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের, একের সাথে সমষ্টির সম্পর্কের সমীকরণ― ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাসের নিরিখে সন্মাত্রানন্দের এই রচনা নিঃসন্দেহে সার্থক।
শেয়ার করুন :